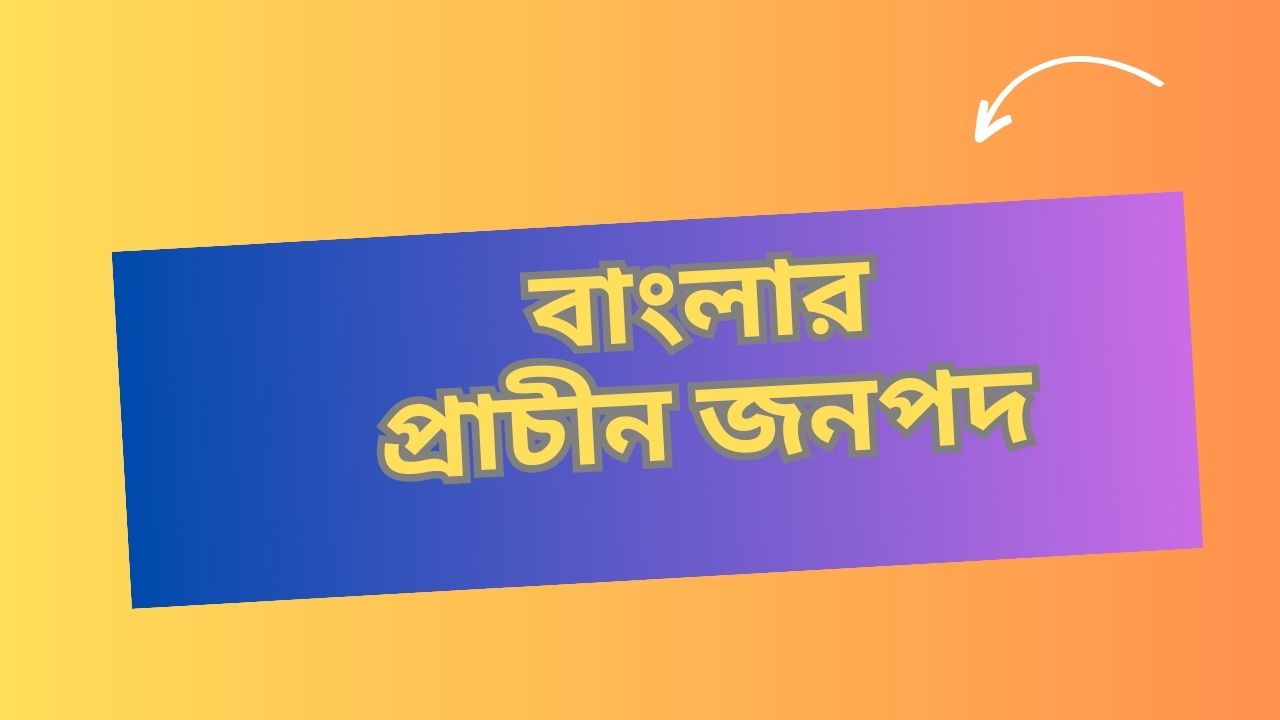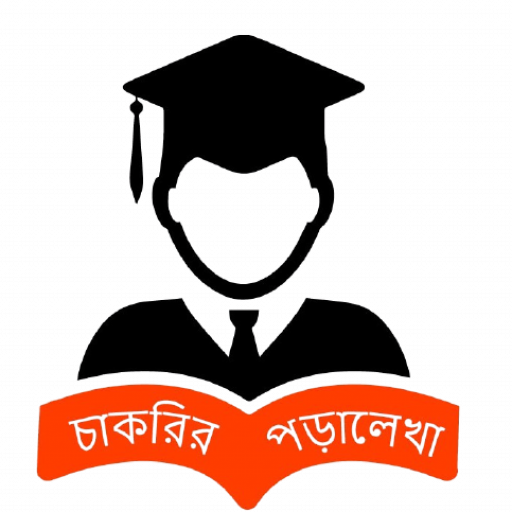বাংলার প্রাচীন জনপদ নিয়ে চাকরি ও ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা সহ বিভিন্ন একাডেমিক পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয়। সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বাংলার প্রাচীন জনপদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা আবশ্যক। এই পোস্টে প্রাচীন বাংলার জনপদ গুলো কি কি, এদের বর্তমান অবস্থান, ও এই জনপদগুলোর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হবে।
বাংলার প্রাচীন জনপদ
বাংলার প্রাচীন জনপদ কী?
প্রাচীনকালে বাংলাদেশে কোনো একক রাষ্ট্র ছিল না। এটি তখন কতকগুলো অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। অঞ্চলগুলো জনপদ নামে পরিচিত ছিল।
বাংলার প্রাচীন জনপদ ও এগুলোর বর্তমান নাম
বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন জনপদ ও প্রাচীন বাংলার জনপদের বর্তমান অবস্থান নিচে উল্লেখ করা হলো-
| প্রাচীন জনপদ | বর্তমান অঞ্চল |
| গৌড় | উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, আধুনিক মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের কিছু অংশ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ |
| বঙ্গ | ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালীর নি¤œ জলাভূমি, ময়মনসিংহ এর পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা, কুষ্টিয়া, বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালীর কিছু অংশ |
| পুণ্ড | বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী ও রংপুর জেলা |
| হরিকেল | সিলেট (শ্রীহট্ট), চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম |
| সমতট | কুমিল্লা ও নোয়াখালী |
| বরেন্দ্র | বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার অনেক অঞ্চল এবং পাবনা জেলা |
| তাম্রলিপ্ত | পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা |
| চন্দ্রদ্বীপ | বৃহত্তর বরিশাল, গোপালগঞ্জ ও খুলনা |
| উত্তর রাঢ় | মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ, সমগ্র বীরভূম জেলা এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা |
| দক্ষিণ রাঢ় | বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলির বহুলাংশ এবং হাওড়া জেলা |
| বাংলা বা বাঙলা | সাধারণত খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী |
প্রাচীন বাংলার জনপদ কয়টি?
উল্লেখ্য, গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, হরিকেল, সমতট, বরেন্দ্র এরকম প্রায় ১৬টি জনপদের কথা জানা যায়।
বাংলার প্রাচীন জনপদ কিছু তথ্য কণিকা
👉 বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদ- পুণ্ড।
👉 ‘বঙ্গ’ নামে দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়- খ্রিস্টপূর্ব ৩ হাজার বছর আগে।
👉 সর্বপ্রথম ‘বঙ্গ’ দেশের নাম পাওয়া যায়- ঋগে¦দের’ ঐতরেয় আরণ্যক’ গ্রন্থে।
👉 সুপ্রাচীন বঙ্গ দেশের সীমা উল্লেখ আছে- ড. নীহাররঞ্জন রায়ের ‘বাঙালির ইতিহাস’ গ্রন্থে।
👉 বাংলার আদি জনপদগুলোর জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল- অস্ট্রিক।
👉 বরেন্দ্র বলতে বোঝায়- উত্তরবঙ্গকে (বগুড়া, রাজশাহী জেলার বৃহৎ অংশ)।
👉 প্রাচীনকালে ‘গঙ্গারিডই’ নামে শক্তিশালী রাজ্যটি ছিল- অনুমান করা হয় গঙ্গা নদীর তীরে।
👉 রাজা শশাঙ্কের শাসনামলের পরে ‘বঙ্গদেশ’ যে কয়টি জনপদে বিভক্ত ছিল- ৩টি; পুÐ্র, গৌঢ় ও বঙ্গ।
👉 বঙ্গ ও গৌড় নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়- ষষ্ঠ শতকে।
👉 হিউয়েন সাঙ এর বিবরণ অনুসারে কামরূপে যে জনপদ ছিল- সমতট।
👉 রাঢ়দের রাজধানী ছিল- কোটিবর্ষ।
👉 প্রাচীন যেসব গ্রন্থে বঙ্গ দেশের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়- ঋগে¦দের ‘ঐতরেয় আরণ্যক’-এর শ্লোকে (২-১-১), মহাভারতে, পতঞ্জলির ভাষ্যে, ওভেদী, টলেমির লেখায়, কালিদাসের ‘রঘুবংশে’ এবং আবুল ফজলের ’আইন-ই আকবরী’ গ্রন্থে।
👉 সমতট রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল- কুমিল্লা জেলার বড়কামতায়।
👉 প্রাচীন রাঢ় জনপদ অবস্থিত- বীরভ‚ম ও বর্ধমানে।
👉 প্রাচীনকালে ‘সমতট’ বলতে বোঝায়- কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলকে।
👉 বর্তমান বৃহৎ বরিশাল ও ফরিদপুর এলাকা প্রাচীনকালে যে জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল- বঙ্গ।
👉 সিলেট প্রাচীন যে জনপদের অন্তর্গত- হরিকেল।
👉 প্রাচীন বাংলায় বাংলাদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল- হরিকেল।
বাংলার প্রাচীন জনপদ পরিচিতি
🔶 গৌড়
বাংলার উত্তরাংশ এবং উত্তরবঙ্গে ছিল গৌড় রাজ্য। সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত গৌড় রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে শশাঙ্ক গৌড় নামে একত্রিত করেন। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ (বর্তমানে অঞ্চল) ছিল শশাঙ্কের সময়ে গৌড় রাজ্যের রাজধানী। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও সন্নিকটের এলাকা গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুলতানী সময় বাংলার উত্তর-পশ্চিমাংশ, বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলের রাজধানী ও ছিল গৌড় নগরী।
🔶 বঙ্গ
ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নি¤œ জলাভূমি এবং পশ্চিমের উচ্চভূমি যশোর, কুষ্টিয়া, নদীয়া, শান্তিপুর ও ঢাকার বিক্রমপুর সংলগ্ন অঞ্চল ছিল বঙ্গ জনপদের অন্তর্গত। সুতরাং বৃহত্তর ঢাকা প্রাচীনকালে বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুরানো শিলালিপিতে ‘বিক্রমপুর’ ও ‘নাব্য’ নামে দুটি অংশের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন বঙ্গ ছিল একটি শক্তিশালী রাজ্যে। ঋদ্বেদের (প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য) ‘ঐতরেয় আরণ্যক’-এ বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া রামায়ণ ও মহাভারতে এবং কালিদাসের ‘রঘুবংশ-এ ‘বঙ’ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমগ্র বাংলা বঙ্গ নামে ঐক্যবদ্ধ হয় পাঠান আমলে।
🔶 সমতট
হিউয়েন সাং এর বিবরণ অনুযায়ী সমতট ছিল বঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বাংশের একটি নতুন রাজ্যে। মেঘনা নদীর মোহনাসহ বর্তমান কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল সমতটের অন্তর্ভুক্ত কুমিল্লা জেলার বড় কামতা এ রাজ্যের রাজধানী ছিল বলে জানা যায়।
🔶 রাঢ়
রাঢ় বাংলার একটি প্রাচীন জনপদ। ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীর হতে গঙ্গা নদীর দক্ষিণাঞ্চল রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত। অজয় নদী রাঢ় অঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। রাঢ়ের দক্ষিণে মেদেনীপুর জেলায় ‘তাম্রলিপি’ ও ‘দণ্ডভুক্তি’ নামে দুটি ছোট বিভাগ ছিল। তৎকালে তা¤্রলিপি ছিল একটি বিখ্যাত নৌবন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।
প্রাচীন বাংলার জনপদ মানচিত্র

প্রাচীন বাংলার জনপদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা
প্রাচীন বাংলার জনপদগুলো আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই জনপদগুলো বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
গুরুত্বের কয়েকটি দিক:
1. রাজনৈতিক গুরুত্ব:
- স্বাধীন রাষ্ট্র: অতীতে বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল।
- রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তি: ধীরে ধীরে এই দেশগুলো একত্রিত হয়ে একটি বৃহৎ রাষ্ট্র গঠন করে।
- শক্তিশালী রাজবংশের উত্থান: শক্তিশালী রাজবংশ যেমন পাল, সেন, বর্মণ ইত্যাদি। এই দেশ থেকে জন্ম।
2. অর্থনৈতিক গুরুত্ব:
কৃষি ও বাণিজ্যের কেন্দ্র। এই সম্প্রদায়গুলি ছিল উর্বর কৃষি অঞ্চল এবং বাণিজ্য কেন্দ্র।
নদী ব্যবস্থা: নদী ব্যবস্থা দেশী ও বিদেশী পণ্য পরিবহন করত।
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি. এই শহরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিল তাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ভিত্তি।
3. সাংস্কৃতিক গুরুত্ব:
ধর্মীয় স্থান: বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন ধর্মের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান এই শহরে অবস্থিত ছিল।
শিল্প: এই শহরগুলিতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলার উন্নত রূপ রয়েছে।
সাহিত্য: প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনেক বিখ্যাত রচনা এই শহরে রচিত হয়েছিল।
4. ঐতিহাসিক গুরুত্ব:
বাঙালি জাতির জন্মস্থান: এই শহরগুলোকে বাঙালি জাতির জন্মস্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
বাংলা ভাষার উৎপত্তি: বাংলা ভাষার উৎপত্তি প্রাচীন বাংলা শহর থেকে।
বাংলার সংস্কৃতির ভিত্তি: এই গ্রামের সংস্কৃতি আজ বাংলার সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করেছে।
আরো পড়ুন: